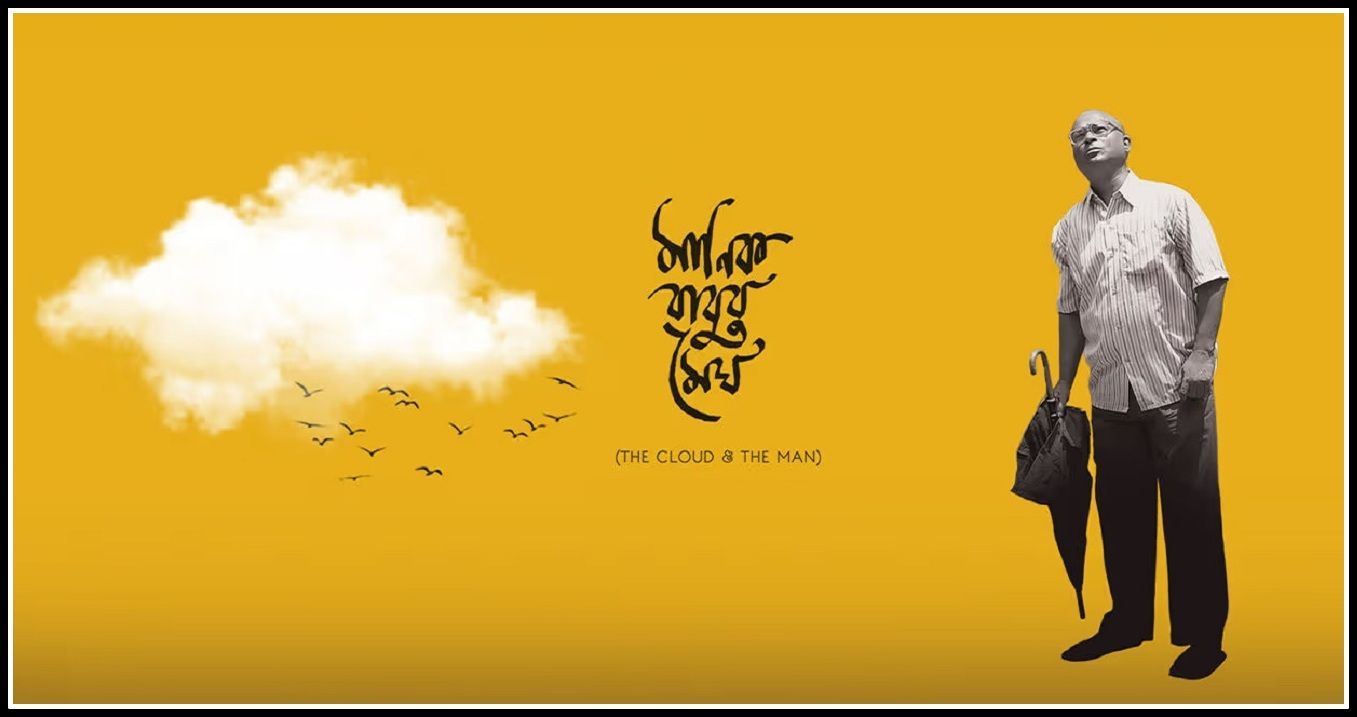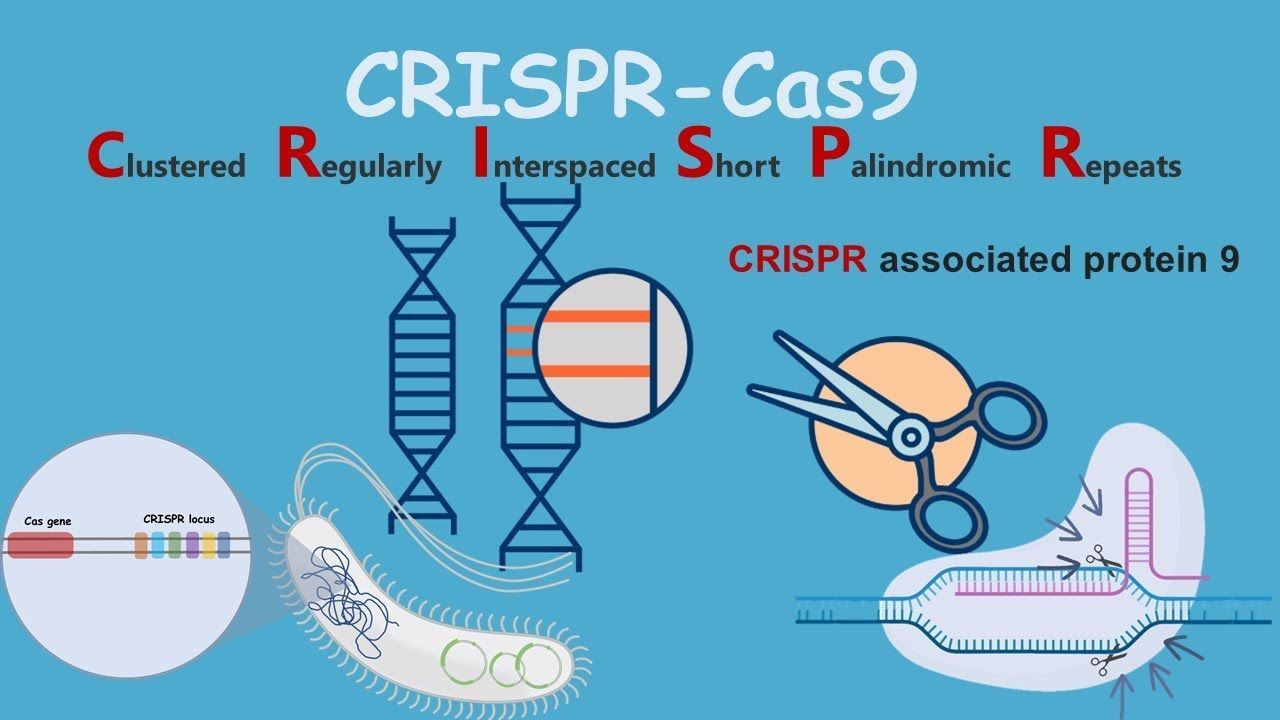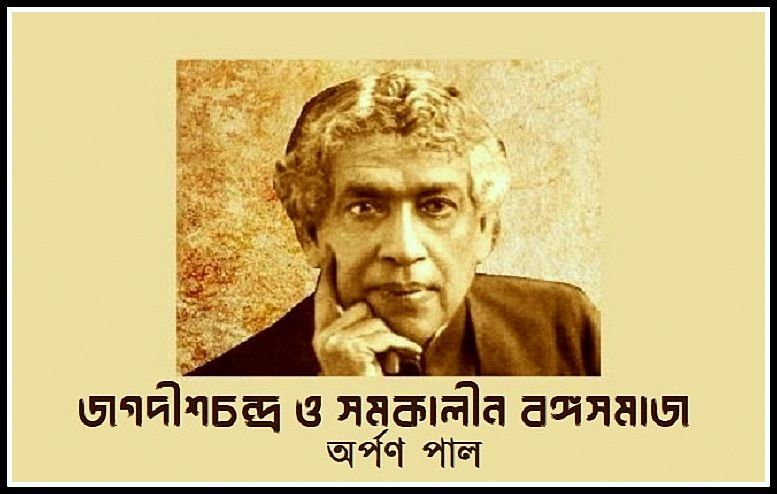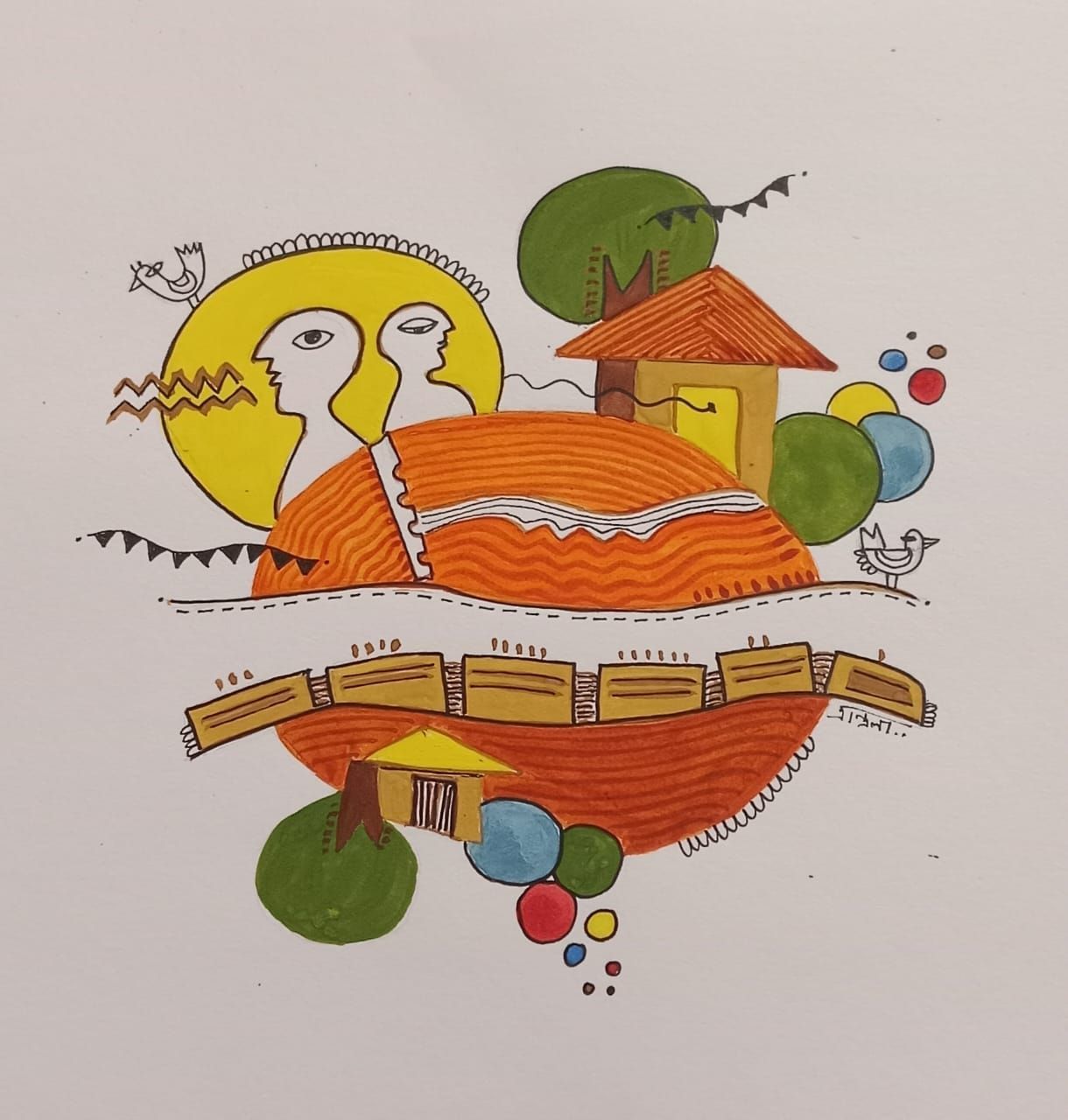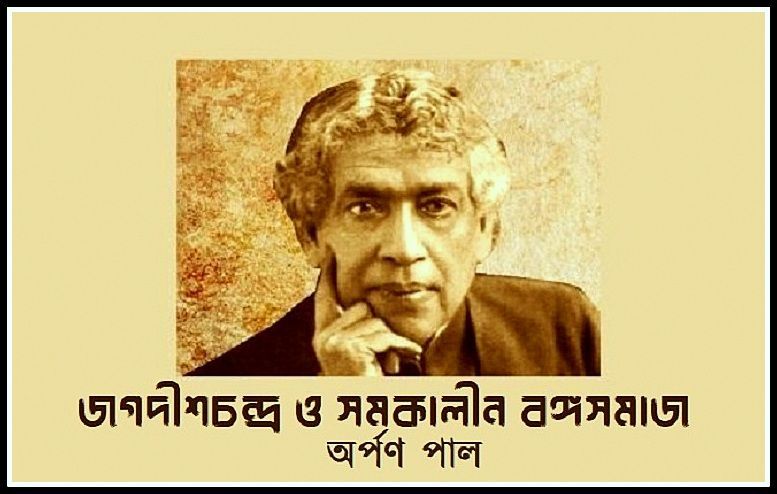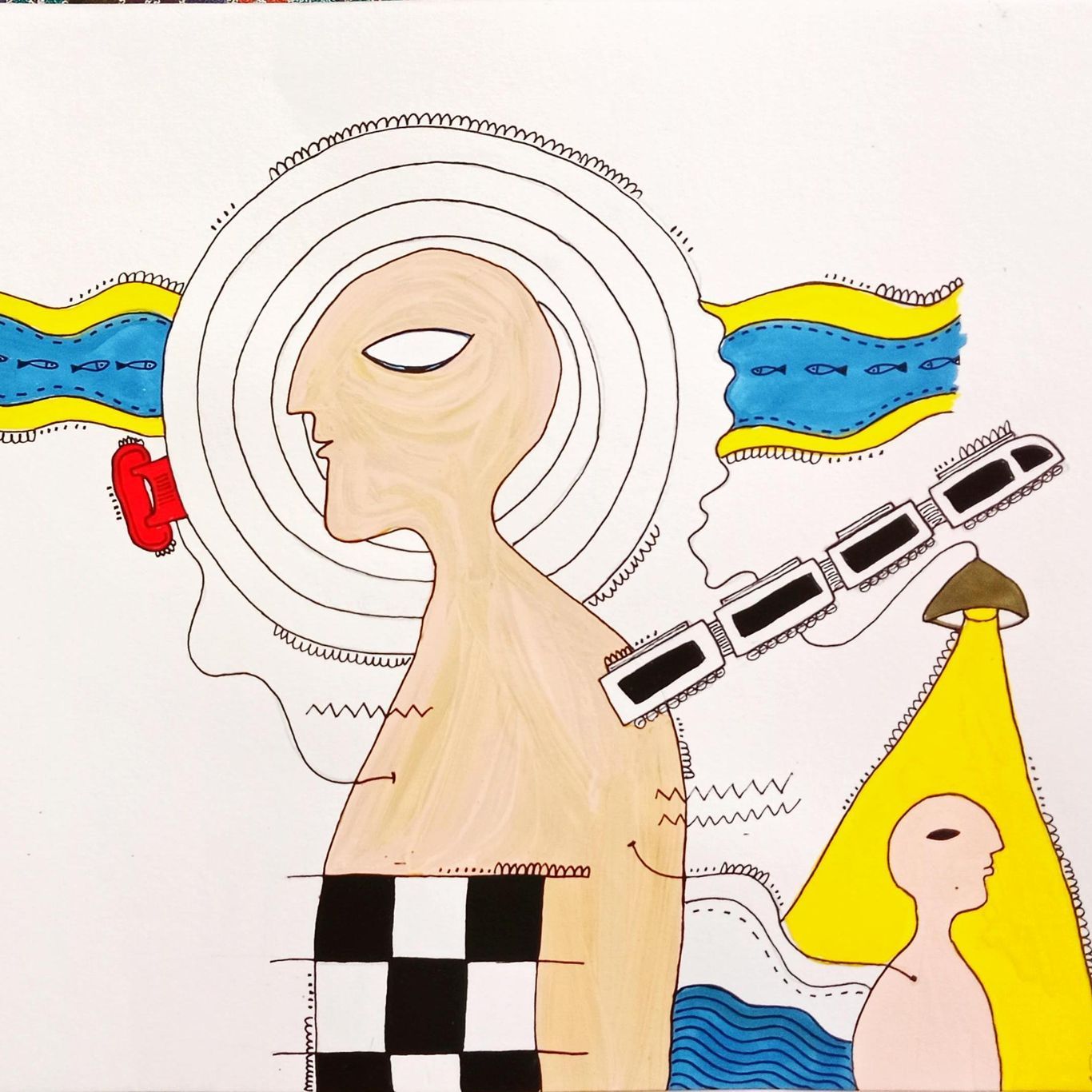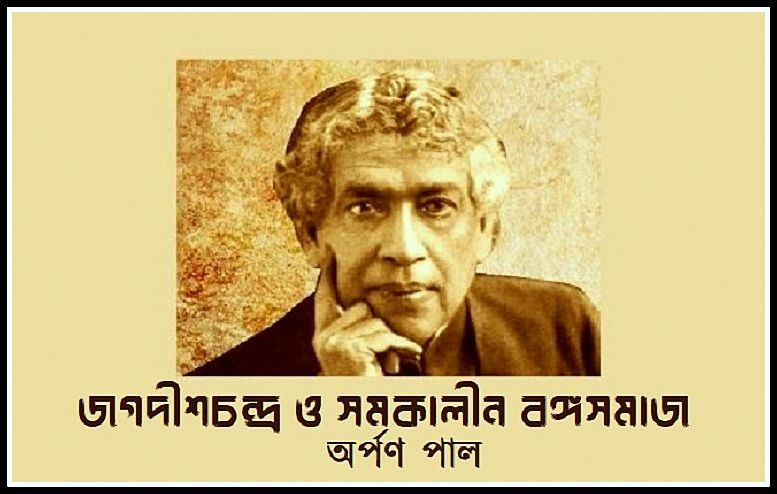জগদীশ-নিবেদিতা সংবাদ (দশম পর্ব)
_1366x1366.jpg?alt=media)
............
পর্ব ১০। বুদ্ধগয়া পর্ব : নিবেদিতা-জগদীশচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের ত্রিবেণীসঙ্গম
১৯০৪ সালের ২০ জানুয়ারি স্বামীজীর জন্মোৎসব পালনের পর নিবেদিতা যাত্রা করলেন লখনউ-এর উদ্দেশ্যে। সঙ্গী হিসেবে নিলেন স্বামী সদানন্দ আর স্বামী শঙ্করানন্দকে (অন্য নামে ব্রহ্মচারী অমূল্য)। বাঁকিপুর থেকে তাঁরা আসেন পাটনায়। প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার প্রতি নিবেদিতার আকর্ষণ ছিল যথেষ্ট, সুতরাং প্রাচীনকালের পাটলিপুত্রকে দেখে মুগ্ধ তিনি তো মুগ্ধ হবেনই। এই শহরে একাধিক স্থানে বক্তৃতা দিলেন, এরই পরবর্তী গন্তব্য হিসেবে স্থির ছিল লখনউ, কিন্তু মাঝখানের দিনগুলোতে কোথায় যাওয়া যায়, সেই কথা ভাবতে-ভাবতে নিবেদিতার মাথায় আসে বুদ্ধগয়ার কথা। তাঁর গুরুজী এখানে এসেছিলেন মাত্রই বছর দুয়েক আগে, সেই ১৯০২ সালের জানুয়ারিতে। ওটাই ছিল স্বামীজীর শেষ ভ্রমণ। সে সময় নিবেদিতা ছিলেন ভারতগামী জাহাজে, ফিরছিলেন লন্ডন থেকে। যে কারণে স্বামীজীর সেই বুদ্ধগয়া সফরে তিনি সঙ্গী হতে পারেননি।
স্বামীজীর মতোই বুদ্ধদেবকে নানা কারণে বেশ পছন্দ করতেন নিবেদিতাও। জীবনের প্রথম পর্যায়েই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বৌদ্ধ ধর্মমতের প্রতি, বিশেষ করে এক অশান্ত সময়ে এডউইন আর্নল্ড-এর ‘লাইট অভ এশিয়া’ বইটি পড়বার পর তিনি যথেষ্ট মানসিক শান্তি আর তৃপ্তি পেয়েছিলেন। পরে স্বামীজীর কাছেও একাধিকবার শুনেছেন বুদ্ধের বাণী, স্বামীজী বৌদ্ধ দর্শনকে পরম শ্রদ্ধা করতেন। নিবেদিতাও বুদ্ধের বাণী থেকে পেতেন পরম শান্তির বাতাস। সুতরাং বুদ্ধগয়া তাঁকে যে টানবে, এতে আশ্চর্যের কী?
সেবারের বুদ্ধগয়া সফরে যদিও তিনি বেশিদিন থাকতে পারেননি। ওখানকার মন্দিরের দেখভাল করেন যিনি, সেই মোহন্তের অতিথি হিসেবে তাঁরা এক ডাকবাংলোয় ছিলেন। সেখান থেকে মিস ম্যাকলাউডকে লেখা এক চিঠি থেকে জানা যায়, নিবেদিতা যথেষ্ট সচেতন ছিলেন ওখানকার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে। যে পরিস্থিতির মধ্যে তিনি নিজেকে জড়িয়ে নেবেন মাস কয়েক পরেই।
বুদ্ধগয়ার যে মূল মন্দির, সেটি হিন্দুদের দখলে থাকবে নাকি তার দায়িত্ব অর্পিত হবে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের হাতে, এ নিয়ে একটা টানাপড়েন চলছিল বেশ কয়েক মাস ধরেই। বৌদ্ধদের নেতা হিসেবে অনাগারিক ধর্মপাল চাইছিলেন এই মন্দিরটিকে নিজেদের দখলে নিতে। অন্যদিকে শৈবদের নেতা মোহন্ত দায়িত্ব ছাড়তে রাজি ছিলেন না, ফলে ঝামেলা গড়ায় আদালত অবধিও। ব্রিটিশ সরকার প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের এই ঝামেলায় না জড়ালেও লর্ড বেন্টিঙ্কের প্রচ্ছন্ন সমর্থন ছিল বৌদ্ধদের প্রতিই। নিবেদিতা, স্বামীজীর দেখানো পথ অনুসরণ করেই মনে করতেন যে ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্ম আসলে হিন্দু ধর্মেরই এক রূপ। বেদান্ত-সমর্থকদের সঙ্গে বৌদ্ধদের অন্তর্লীন সাদৃশ্য অনুধাবন করেছিলেন স্বামীজী।
সুতরাং নিবেদিতা প্রকাশ্যেই সমর্থন জানালেন হিন্দু মোহন্তের দাবিকে। কলকাতায় ফিরে ফেব্রুয়ারির ষোল তারিখে তিনি ‘বুদ্ধগয়া’ নামে যে বক্তৃতাটি দিয়েছিলেন সেখানেও আলোচনা করেন এই প্রসঙ্গে। কলকাতার পাশাপাশি কাশী বা লখনউতেও তিনি যে বক্তৃতাগুলি দেন, সেগুলির মধ্যেও কয়েকটিতে উত্থাপিত হয়েছিল এ-প্রসঙ্গ।
প্রথমবার বুদ্ধগয়ায় আসবার মাস দুয়েক পরে, মার্চ মাসে কাশী যাওয়ার পথে আরও একবার এখানে আসেন তিনি, সেবারে সঙ্গে ছিলেন শ্রীমতী সেভিয়ার। সেবারেও মোহন্তের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়। বুদ্ধগয়ার নিয়ে পরে কলকাতায় এপ্রিলের এক তারিখেও তিনি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। পাশাপাশি কয়েকটি পত্রিকাতেও লিখেছিলেন বেশ কিছু লেখা, সবগুলোরই মূল বক্তব্য এটাই যে বুদ্ধগয়ার থাকা উচিত হিন্দুদের অধিকারে। শুধু নিজে লিখেই ক্ষান্ত হননি, স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক স্যামুয়েল র্যাডক্লিফ-কেও উৎসাহিত করে তাঁকে দিয়েও লিখিয়ে নিয়েছিলেন সমর্থন-নিবন্ধ। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাদান সরবরাহও করেছিলেন তিনি।
২.
বুদ্ধগয়ায় বড় একটা দল নিয়ে নিবেদিতা যাত্রা করেন অক্টোবর মাসে। তবে এর আগে তিনি আরও একটি সফর সেরে এসেছিলেন। সেটার শুরু মে মাসের তিন তারিখে, তখন গ্রীষ্মের ছুটিরও সূচনা। ব্রিটিশ দম্পতি মিস্টার জেমস হেনরি সেভিয়ার আর মিসেস শার্লট এলিজাবেথ সেভিয়ার আলমোড়ায় নির্জন পাহাড়ের কোলে শান্তির খোঁজে বানিয়েছেন এক আশ্রম, সেখানেই দলবলসহ উঠেছিলেন নিবেদিতা। ছোট দল, সদস্য তাঁকে বাদ দিয়ে চারজন; সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র, সিস্টার ক্রিস্টিন আর লাবণ্যপ্রভা বসু।
এখানে নিবেদিতা পেয়েছিলেন কাঙ্ক্ষিত পাহাড়ি নির্জনতা। পাশাপাশি সেভিয়ার দম্পতির উষ্ণ আতিথেয়তা, স্বামীজীর শিষ্য স্বরূপানন্দ আর বসু দম্পতির সঙ্গ। স্বামী স্বরূপানন্দের ডায়েরিতে আছে একটি দিনের উল্লেখ:
১৯০৪-এর মে মাসের ১৬ তারিখে: ‘Dr. and Mrs. J. C. Bose, his sister, Nivedita and Greenstidel arrive and go back on 16th June.’ (লোকমাতা নিবেদিতা, শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ১ম খণ্ড ১ম পর্ব, ২৪৯ পৃ। এখানে হিজ সিস্টার বলতে লাবণ্যপ্রভা বসু) সব মিলিয়ে নিবেদিতার সময় বেশ ভালোই কাটছিল। জগদীশচন্দ্র এই শান্ত নির্জন পরিবেশেই শুরু করলেন তাঁর ‘রেসপন্স ইন লিভিং অ্যান্ড নন-লিভিং’ বইটি লেখবার কাজ। সেটা মে মাসের ১৭ তারিখ।
সবাই মিলে কলকাতা ফিরলেন জুনের ২৩ তারিখে। আবার কর্মব্যস্ত জীবন। জগদীশচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে পড়লেন তাঁর বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজে।
৩.
মহালয়ার দিন বিকেলে, অক্টোবরের ৮ তারিখে পুজোর ছুটির শুরুতেই একটা বড়সড় দল নিয়ে নিবেদিতা যাত্রা করলেন বুদ্ধগয়ার উদ্দেশ্যে। এবারে দলের সদস্যরা; সস্ত্রীক জগদীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক ও নিবেদিতার গুণগ্রাহী এস কে র্যাটক্লিফ ও তাঁর স্ত্রী, স্বামী সদানন্দ, ত্রিপুরার কর্নেল মহিম ঠাকুর, সিস্টার ক্রিস্টিন, স্বামী শঙ্করানন্দ এরকম সব মিলিয়ে কুড়ি জন। এই কুড়ি জন কারা-কারা, তা নিয়ে কিছু দামি তথ্য পাওয়া যায় শঙ্করীপ্রসাদ বসুর একটি গদ্যে। এই গদ্যটি আছে দেবাঞ্জন সেনগুপ্তর ‘নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ: এক বিতর্কিত সম্পর্কের উন্মোচন’, (গাংচিল প্রকাশনা) ৮৮ পাতায়।
এই বই থেকে উদ্ধৃতি:
‘নিবেদিতার পত্র অনুযায়ী দলে ছিলেন কুড়িজন। কে কে ছিলেন, নানা তালিকা অনুয়ায়ী আমরা দিয়ে দিচ্ছি। স্যার যদুনাথের তালিকায়— ভগিনী নিবেদিতা, ডা. জগদীশচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী সদানন্দ ও ব্রহ্মচারী অমূল্য (স্বামী শঙ্করানন্দ)। আত্মপ্রাণার তালিকায় বাড়তি নাম-- মথুরানাথ সিংহ। মুক্তিপ্রাণার তালিকায় বাড়তি নাম— শ্রীমতী অবলা বসু, সিস্টার ক্রিস্টিন, মি. ও মিসেস র্যাটক্লিফ। লিজেল রেমঁর তালিকায়— ত্রিপুরার রাজকুমার, ইন্দ্রনাথ নন্দী, চন্দ্রকুমার দে। রেমঁ, রবীন্দ্রনাথ পত্নীর কথা লিখেছেন, মনে হয় অসাবধানে ‘মিস্টার’-এর আগে ‘মিসেস’ পড়ে গেছে রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখ করার কালে। রথীন্দ্রনাথ ত্রিপুরার রাজকুমারের (দ্বিতীয় রাজকুমার) নাম জানিয়েছেন, ব্রজেন্দ্রকিশোর (লালুকর্তা), এবং বাড়তি নাম দিয়েছেন— তাঁর সহপাঠী সন্তোষচন্দ্র মজুমদার ও ত্রিপুরার কর্ণেল মহিম ঠাকুর। স্বামী শঙ্করানন্দের সঙ্গে কথোপকথনের রেমঁকৃত নোটে দেখেছি, তিনি মি. ও মিসেস র্যাটক্লিফ, ইন্দ্রনাথ নন্দী, চন্দ্রনাথ দে’র নাম দিয়েছিলেন। এইসঙ্গে অরবিন্দমোহন বসু জিন হারবার্টকে জানিয়েছিলেন, তিনিও দলে ছিলেন। নামগুলি যদি ঠিক হয়, তাহলে আমরা মোট আঠার জনের নাম পাচ্ছি।’ (মূল লেখাটির নাম ‘নিবেদিতার পত্রে রবীন্দ্রনাথ এবং প্রাসঙ্গিক তথ্য’, দেশ, ৭ পৌষ ১৯৭৪। পৃ ৭৭৩)
সব মিলিয়ে বোঝাই যাচ্ছে যে দল বেশ বড়ই। পরে পাটনা থেকে যদুনাথ সরকার আর মথুরানাথ সিংহ এই দলে যোগ দেন। এই দলের কনিষ্ঠ সদস্য ছিলেন রথীন্দ্রনাথ।
যাওয়ার আগেই ঠিক হয়েছিল যে তাঁরা বুদ্ধগয়ার মোহন্তের অতিথি হবেন। সেইমতো যাওয়ার পর অতিথিশালার বিরাট ভবনের তিনতলার ঘরগুলোয় সকলের থাকবার ব্যবস্থা হল। যদিও অতিথিরা ঘরে থাকবার চেয়ে লম্বা টানা বারান্দাতেই সময় কাটাতেন বেশি। খাওয়াদাওয়ার কোনও অসুবিধা ছিল না; ভালো দুধ, ঘি, ফলমূল, আরও নানারকমের খাদ্য সারাক্ষণই মজুত থাকত।
প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণার নিবেদিতা জীবনী থেকে পাই এইসময়কার দিনগুলির বিবরণ: ‘প্রতিদিন ওয়ারেনের ‘বৌদ্ধধর্ম’ পুস্তক হইতে অথবা এডউইন আর্নল্ডের ‘লাইট অব এশিয়া’ হইতে নিবেদিতা পড়িতেন; রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে গান ও আবৃত্তি করিতেন। দিনের বেলা তাঁহারা মন্দির চত্বরে পায়চারি করিতেন, অথবা আশেপাশের গ্রামগুলিতে বেড়াইতে যাইতেন। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যখন চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া আসিত, গোধূলির ধূসর আলোকে সকলে বোধিদ্রুমতলে নীরবে উপবেশনপূর্বক সমগ্র অন্তর দিয়া স্থানটির মাহাত্ম্য উপলব্ধির চেষ্টা করিতেন।’ (২৬২ পৃ)
আরও একটি উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে, ‘এক সন্ধেয় নিবেদিতা প্রস্তাব করিলেন, ‘চলুন, আমরা সুজাতার বাড়ি দেখে আসি। সেখানে কোন ভগ্নাবশেষ বা ধ্বংসস্তূপ নেই। জায়গাটির চারদিক ঘাসে ঢাকা, কিন্তু ভারী পবিত্র। সুজাতাই ছিলেন আদর্শ গৃহিণী, কারণ তিনিই বুদ্ধদেবকে যথাসময়ে আহার্য দিয়েছিলেন।’ (মুক্তিপ্রাণা, ২৬৩ পৃ)
রবীন্দ্রনাথের কিশোর পুত্র রথীন্দ্রনাথ সেই যাত্রায় তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁর ‘পিতৃস্মৃতি’ থেকে পাই আরও কিছু বর্ণনা: ‘রোদ পড়ে গেলে সন্ধের দিকে সকলে মিলে মন্দির দেখতে যাই। ত্রিপুরার মহিম ঠাকুর ও লালুকর্তা দুজনেরই ফোটো তোলার শখ; তাঁদের সঙ্গে ছোটো বড়ো নানা রকম ক্যামেরা ছিল; দিনের আলো থাকতে কোনো সময় গিয়ে তাঁরা বহু ফোটো তুলে রেখেছিলেন। (সে ফোটোগুলি আছে কিনা জানি না)। মন্দির দেখা হলে আমরা মন্দিরের পিছনের দিকে বোধিদ্রুমের নিকটে গিয়ে বসলুম। তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে, মন্দিরের গায়ে গবাক্ষগুলিতে প্রদীপ জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। চার দিক নিস্তব্ধ; তার মধ্যে কানে এল ‘ওঁ মণিপদ্মে হুঁ’— বৌদ্ধমন্ত্রের মৃদুগম্ভীর ধ্বনির আবর্তন। কয়েকটি জাপানি তীর্থযাত্রী এই মন্ত্র আবৃত্তি করতে করতে মন্দির প্রদক্ষিণ করছেন; আর প্রতি পদক্ষেপে একটি করে ধূপ জ্বেলে রেখে দিয়ে যাচ্ছেন। কী শান্ত তাঁদের মূর্তি। কী গভীর তাঁদের ভক্তি। ইষ্টপূজার কী অনাড়ম্বর প্রণালী। অনতিপূর্ব মন্দিরের ভিতরে বুদ্ধমূর্তির পুরোহিতদের কর্কশ ঢাক ঢোল বাজিয়ে আরতি দেখে এসেছিলাম। আমাদের মনে এই কথাটাই জাগল, ভগবান এঁদের মধ্যে কার পূজা খুশি হয়ে গ্রহণ করলেন? মন্দিরের পরিবেশ ছেড়ে কারো আর উঠতে ইচ্ছা হয় না। অনেক রাত পর্যন্ত জগদীশচন্দ্র, ভগিনী নিবেদিতা ও পিতৃদেব বৌদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ ইতিহাস নিয়ে নিবিষ্ট মনে আলোচনা করতেন। নিবেদিতা এক-একটি তর্ক তোলেন আর রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করেন তার যথাযোগ্য সমাধানে পৌঁছতে। আমরা অন্যেরা তাঁদের প্রশ্নোত্তর তর্ক-বিতর্ক মুগ্ধ হয়ে শুনে যাই। আমার বিশ্বাস, এই বুদ্ধগয়া-সন্দর্শনের ফলে উত্তরকালে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যে পিতৃদেবের অন্তরের আকর্ষণ প্রগাঢ় গভীর হয়ে উঠেছিল। শান্তিনিকেতনে ফিরে এসে আমাকে তিনি ধম্মপদ আগাগোড়া মুখস্থ করতে দিয়েছিলেন। পালি পড়াও শুরু হল এবং পিতারই আদেশক্রমে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত তর্জমার দুঃসাহসে প্রবৃত্ত হলুম।’
‘বুদ্ধদেবের বোধিলাভের পূতস্থান বুদ্ধগয়ায় জগদীশচন্দ্র, নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ তিন মনীষীর একত্র সমাগমে অপূর্ব এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল। মাত্র দু-তিন দিনের তীর্থবাস, কিন্তু তারই মধ্যে কত গল্প, কত আলোচনা, কত পরামর্শই না হয়েছিল। বড়ো দুঃখ যে তার আজ কোনো অনুলিপি নেই। সেই অল্প বয়সে বুদ্ধগয়ার মাহাত্ম্য বা বয়স্কদের আলাপ-আলোচনা সম্পূর্ণ বোঝবার ক্ষমতা ছিল না। না থাকলেও এই তীর্থস্থানে দুর্লভ সৎসঙ্গে ত্রিরাত্রিবাসের স্মৃতি আমার মানসপটে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। (পিতৃস্মৃতি, ২২১- ২২২ পাতা) এছাড়াও ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকারের ‘Reminiscences of Sister Nivedita’ নামে একটি পাঁচ পৃষ্ঠাব্যাপী স্মৃতিকথা প্রকাশ পেয়েছিল ‘প্রবুদ্ধ ভারত’-এর জানুয়ারি, ১৯৪৩ সংখ্যায়। সেই স্মৃতিকথাতেও রয়েছে এই সফরের খুঁটিনাটি খবর।
ফেরার পথে সকলে একসঙ্গে ফেরেননি। ১২ অক্টোবর সকলে গয়া স্টেশনে আসেন এবং বিভিন্নজন আলাদা আলাদা দিকে গমন করেন। জগদীশচন্দ্র, নিবেদিতা আর রবীন্দ্রনাথের এটাই একমাত্র যৌথ সফর। যদিও এই সফরে নিবেদিতার আসল লক্ষ বা কাঙ্ক্ষিত ইচ্ছে পূরণ হয়নি; যার পেছনে একটা বড় কারণ ছিল রবীন্দ্রনাথ ছিলেন বৌদ্ধদের সমর্থক, মানে নিবেদিতার বিরোধী। আর সেই মানুষটিকেই তিনি বুঝতে না পেরে নিজের সফর-সঙ্গী করেছিলেন!
এরপরে যদিও তাঁরা একত্রে সময় কাটাবেন, তবে কোনও ঐতিহাসিক স্থানে না, রবীন্দ্রনাথের যৌবনের উপবন শিলাইদহে। তবে সে আলোচনা, পরের পর্বে।
............
আগের পর্ব পড়ুন : জগদীশ-নিবেদিতা সংবাদ (নবম পর্ব)